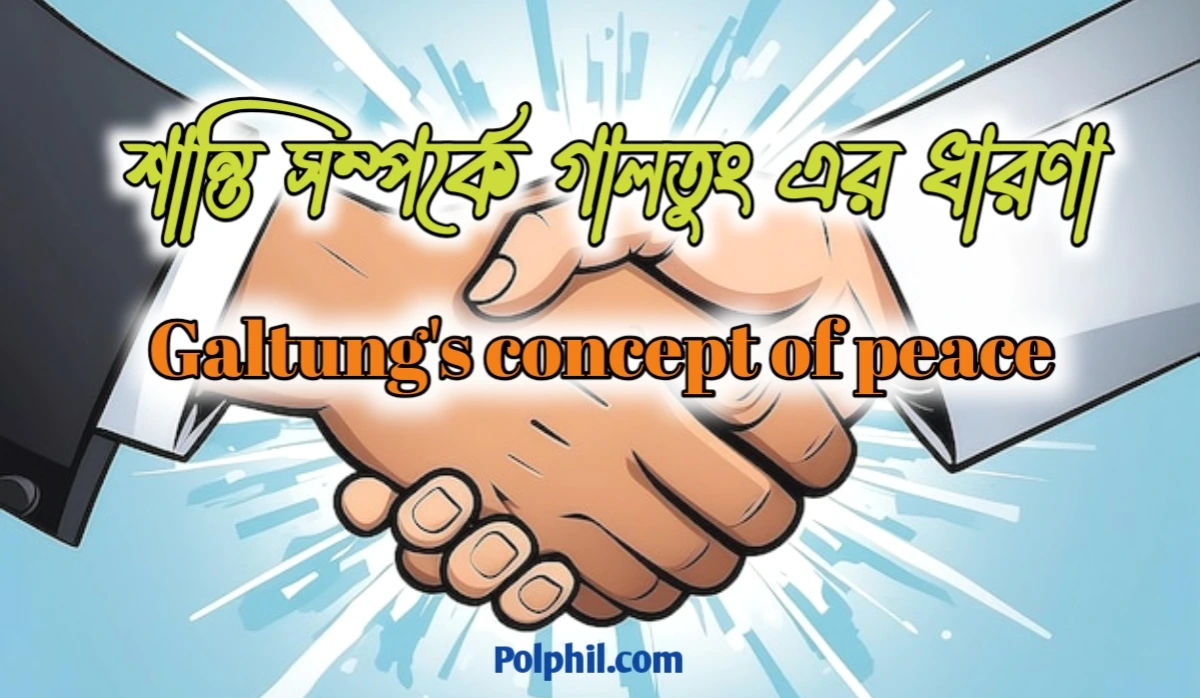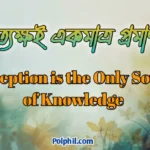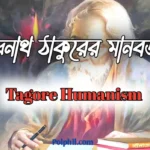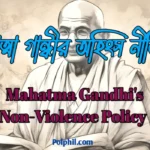শান্তি হলো এমন এক প্রকার অবস্থা যা প্রত্যেকটা রাষ্ট্র তথা ব্যক্তি, সমস্ত প্রকারেই কাম্য একটি বিষয়। শান্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে শান্তি সম্পর্কে গালতুং এর ধারণা (Galtung’s concept of peace) অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।
শান্তি সম্পর্কে গালতুং এর ধারণা | Galtung’s concept of peace
গালতুং শান্তির সাথে ঔষধের একটা যোগসূত্র উপস্থাপন করেন। পরবর্তী সময়ে শান্তি অধ্যায়ন একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
গালতুং তার বর্ণনার প্রথম দিকে শান্তি অধ্যায়নকে বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দর্শন, আদর্শ রাজনীতির পক্ষপাতিত্ব গতানুগতিক শান্তি চিন্তা করেছেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শান্তিকে তিনি অবৈজ্ঞানিক ও মূল্যবোধযুক্ত এবং উদ্দেশ্য প্রভাবিত হিসেবে ভাবার কথা বলেছেন।
শান্তি সম্পর্কে গালতুং এর ধারণায় (Galtung’s concept of peace) শান্তি বিষয়টি তার কাছে অনেকটা শক্তির সাম্যের উপর নির্ভরশীলতার মত। মূলত বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোই বিশেষ করে উন্নত পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলোই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। গতানুগতিক শান্তি বিষয়ে চিন্তা ভাবনাতে আসলে কোন কাজ হবে না। আদর্শবাদী গবেষকরা অবশ্য বিশ্ব পরিস্থিতি ও সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার উপর আলোকপাত করে।
শান্তি আলোচনায় বিভিন্ন বিষয় যেমন রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন, বিজ্ঞানের বৃত্তিমূল ও পেশাগত অঙ্গীকার সমূহ সমূহ স্থান পায়।
‘The Journal of Peace Research’ নামক একটি জার্নালে দু ধরনের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন মিথিলাকে পর থেকে যেখানে তিনি যুদ্ধ ও সংঘাতের অনুপস্থিতিকে শান্তি হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেন, “Negative peace being the adsence of war and actual physical violence.” এবং অন্যদিকে ইতিবাচক শান্তিকে মানবিক সমাজের সাথে যুক্ত বলেছেন এবং সে ক্ষেত্রে তিনি, “Positive peace initially described as the integration at human society.” বলেছেন।
শান্তি সম্পর্কে গালতুং এর ধারণায় (Galtung’s concept of peace) গালতুং এর এই দু’রকম উক্তির একদিকে যেমন ওরাযজ্ঞতা পূর্ণ বিশ্বের চিত্র রয়েছে এবং অন্যদিকে রয়েছে চিরাচরিত দুঃখ বিরোধী শর্তের উপযোগিতা। যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়টি অবশ্য পরস্পর সম্পর্কিত তবে গালতুং এর মতে সমাজের একটি দলের সদস্য হিসেবে পারস্পরিক ক্রিয়াকর্মে আবদ্ধ থাকে এবং বাস্তব জীবনে সম্প্রতি স্থাপন করা অত্যন্ত মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত বিদ্যমান থাকলেও তাদের মধ্যে ঐক্য একটা স্বয়ংক্রিয় বিষয় বিশেষত গালতু মনে করেন শান্তি যদি তার উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হয় হলো তো শান্তি গবেষক প্রযুক্তিবিদ ও ডাক্তারদের মত রাজনীতির স্বাস্থ্য রক্ষা করতে সক্ষম হবে
জোহান গালতুং এর মতে শান্তির শর্ত সমূহ
শান্তি সম্পর্কে গালতুং এর ধারণাতে (Galtung’s concept of peace) জোহান গালতুং (Johan Galtung) শান্তির জন্য পাঁচটি শর্তের উল্লেখ করেছেন যে শান্তি তথ্যগুলো এমন শর্ত সমূহকে বোঝায় যা প্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রথমত ভারসাম্য (Symmetry), সাদৃশ্য (Homology),সামঞ্জস্যপূর্ণতা (Symbiosis), শক্তির ভারসাম্য (Entropy) এবং প্রতিষ্ঠান নির্মাণ (Institution Building)।
সাদৃশ্য (Homology)
মূলত সাদৃশ্য কথার অর্থ হলো একপ্রকার মিল। গালতু তার দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সাদৃশ্যকে উপস্থাপন করেছে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। কারণ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে অদৃশ্য না থাকলে একে অপরের সাথে ভেদাভেদ রোগ আরো হয়ে ওঠে তাই তাদের মধ্যে সাদৃশ্যতা একেবারে আবশ্যক শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্থাৎ শান্তি হলো দুটো রাষ্ট্রের কাঠামোগত অভিন্নতা আর্থসামাজিক উন্নয়ন সরকার এবং সংস্থাসমূহ সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের ইঙ্গিত করে।
দুটি দেশের লোকজন কমবেশি এবং তাদের ভাষাগত পার্থক্য ইত্যাদি নানা কারণে তাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য লক্ষ্যণীয় হয় কিন্তু যদি শেষ হবে বৈসাদৃশ্য না থাকে তাহলে সাধারণ বিষয়গুলো একে অপরকে বুঝতে সাহায্য করে এবং হল তো তাদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এমন সম্পর্ক না থাকার কারণে শান্তি প্রতিষ্ঠা বিঘ্নিত হয় তাই প্রাচ্য প্রাচ্যই থেকে যায় এবং পশ্চিমা পশ্চিমা থেকে যায় এ দুটি কখনো আর একত্রিত হয়। সুতরাং শান্তি স্থাপন করতে হলে দুটি রাষ্ট্র বা দুই মহাদেশের মধ্যে সাদৃশ্য গুলো খুঁজে বের করা অত্যন্ত আবশ্যক।
ভারসাম্য (Symmetry)
ভারসাম্য অর্থাৎ দুটো রাষ্ট্রের মধ্যে এক প্রকার সমঝোতা তৈরি করা। একটি রাষ্ট্র যদি আয়তনের, জনসংখ্যা এবং সম্পদে অন্য রাষ্ট্রের থেকে বড়ো হয় তবে তাদের মধ্যে ভারসাম্যহীন সম্পর্ক গড়ে উঠবে। কারণ ছোট রাষ্ট্রগুলো বড় রাষ্ট্রগুলোকে ভয়ের চোখে দেখবে এবং প্রত্যেকটা মুহূর্তে বড় রাষ্ট্রগুলো ছোট রাষ্ট্রের উপর নানা রকম ভাবে চাপ সৃষ্টি করে থাকলে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে, ভারসাম্যহীন সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে বহিঃশক্তিকে আমন্ত্রণ জানাবে।
তাই শান্তি স্থাপনা করতে, শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে অবশ্যই দুটো রাষ্ট্রের মধ্যে ভারসাম্যকে বজায় রাখতে হবে। এই ভারসাম্যহীন সম্পর্ক কেবল অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তির মাধ্যমেই সমাধান করা সম্ভব হবে।
শক্তির ভারসাম্য (Entropy)
দেশের সম্পর্ক তাদের জনগণের পারস্পরিক মেলবন্ধনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে এবং আবশ্যিকভাবে সরকারি, বেসরকারি এবং বিভিন্ন দপ্তরের নিয়ম নীতিতেও বিদ্যমান থাকবে। শক্তির ভারসাম্য বলতে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় রকম ক্ষেত্রে বিদ্যমান সহযোগিতাকে বোঝানো হয়।
দুটি দেশের সম্পর্কের ওঠানামার উপর জনগণের সম্পর্ক টিকে থাকে। দুটি দেশের সম্পর্ক ভালো হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত হল দুটি দেশের মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বিনিময়। মানুষের শত্রুতা রাষ্ট্রীয় শত্রুতার দ্বারা পরিগণিত হয় না। যেমন পাকিস্তানের অনেক মানুষ যারা ভারতে কর্মসূত্রে, বিভিন্ন রকম আত্মীয়তার কারনে বসবাস করে থাকেন।আবার অনেক ভারতীয় কর্মসূত্রে অথবা আত্মীয়তা বসত পাকিস্তানে যাতায়াত করে থাকে।
সামঞ্জস্যপূর্ণতা (Symbiosis)
সামঞ্জস্যপূর্ণতা হল এমন যার দ্বারা একে অপরের উপর নির্ভরশীলতাকে বুঝে থাকি। সামঞ্জস্যপূর্ণতা বলতে দুটি সত্তার মিলকে উল্লেখ করা যায়। একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য একটি রাষ্ট্রের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণতার সম্পর্ক বলতে পারস্পরিক সহযোগিতাকেই নির্দেশ করা হয় । যেমন- একটি দেশ অন্য একটি দেশের সাহায্য, সহযোগিতা এবং আদান-প্রদান বা বিনিময় ব্যতিরেকে সাফল্য লাভে অনেকটাই বিঘ্নিত হয়ে থাকে।
কোন দেশের উৎপাদন অথবা অগ্রগতির জন্য পাশাপাশি দেশ থেকে বিভিন্ন কাঁচামাল এবং নানা রকম প্রযুক্তির দরকার হয়ে থাকে। আবার অন্যভাবে, একটি দেশের সাথে অন্য দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বা যাতায়াতের জন্য যোগাযোগের মাধ্যম প্রয়োজন হয়। জলপথে যেমন বাণিজ্যিক জাহাজ যাতায়াতের জন্য বিভিন্ন দেশের নদীগুলোর উপর নির্ভরশীল হতে হয়। এইরূপ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে আদান প্রদানের সম্পর্ক তা হল একপ্রকার সামঞ্জস্যপূর্ণতার সম্পর্ক।
প্রতিষ্ঠান নির্মাণ (Institution Building)
প্রতিষ্ঠান হল এমন একটা জায়গা যা কোন কিছুর মানদণ্ডকে নিশ্চিত করে। প্রতিষ্ঠান নির্মাণ বলতে রাষ্ট্রের একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করাকে বোঝানো হয়। যে প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। এটি রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হবে। প্রতিষ্ঠানগুলি কিছু নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া এবং কার্যপ্রণালী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। রাষ্ট্র তার সার্বভৌমত্বের কিছু ক্ষমতা এই প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে থাকে। যে কারণে এই প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেকার বিরোধ নিষ্পত্তি করে ও শান্তিকে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্বভার বহন করে।
উপসংহার
পরিশেষে বলা যায়,শান্তি সম্পর্কে গালতুং এর ধারণা (Galtung’s concept of peace) দৃষ্টান্তকারী আলোচনা গুলির মধ্যে অন্যতম। যেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় রূপে আলোচিত হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটা দেশ তথা রাষ্ট্রের এবং সমস্ত ব্যক্তি মানুষের মধ্যে এই শান্তির বাতাবরণ তার নির্বিঘ্নতাকে অক্ষুন্ন রাখে। বস্তু যা আমাদের কাছে কাম্য হয়ে থাকে।
তথ্যসূত্র (References)
- Conflict Resolution and Gandhian Ethics –Thomas Weber, Gandhi Peace Foundation, New Delhi, 1991.
- Peace Education: The Concept, Principles and Practices around the World – (eds.) Gabriel Solomon and Baruch Nevo, .
- Comprehensive Peace Education—Betty Reardon, Teachers College Press, 1988.
- Philosophical Perspectives of Peace – Howard P. Kainz
- Peace, War and Defence – (ed.) Johan Galtung
- Internet Sources
প্রশ্ন – Johan Galtung এর শান্তি সম্পর্কিত একটি উক্তিটি লেখ।
উত্তর – Johan Galtung এর শান্তি সম্পর্কিত একটি উক্তিটি হল “Peace is a social goal which is complier but not impossible.” শান্তি হচ্ছে একটি সামাজিক লক্ষ্য যেটি জটিল কিন্তু অর্জন করা অসম্ভব নয়।
প্রশ্ন – Albert Einstein এর শান্তি সম্পর্কিত অভিমত লেখ।
উত্তর – Albert Einstein এর শান্তি সম্পর্কিত অভিমতটি হল “Peace is not only the absence of war , but also the presenceof justice.” শান্তি সম্পর্কিত অভিমত হল শান্তি কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহ বিহীন অবস্থায় নয় বরং এটি ন্যায় বিচারের স্বরূপ।
- প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ চার্বাকদের উক্তিটি ব্যাখ্যা কর | Perception is the Only Source of Knowledge
- ব্যাপ্তি গ্রহের উপায় গুলি কি কি | What are the Ways to Identify of Vyapti
- চিরস্থায়ী শান্তি সংক্রান্ত কান্টের মতবাদ | Kant’s Doctrine of Perpetual Peace
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবতাবাদ | Rabindranath Tagore Humanism
- মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো | Features of Mahatma Gandhi’s Non-Violence Policy