বাক্য এবং বচনের মধ্যে কিছু বিষয়ে মিল থাকলেও বাক্যকে কখনোই বচন বলা হয় না। সুতরাং সেদিক থেকে বাক্য ও বচন এর মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বাক্য ও বচনের মধ্যে পার্থক্য উদাহরণ সহ (Difference between Proposition and Sentence) তাই আলোচনা করা প্রয়োজন।
বাক্য ও বচনের মধ্যে পার্থক্য | Difference between Proposition and Sentence
বাক্য ও বচনের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। তবে সব বচন বাক্য হলেও সব বাক্য কিন্তু বচন নয়। সব বাক্যকে বচনে প্রকাশ করা যায় না। একমাত্র ঘোষক বাক্য বচন প্রকাশ করে।যুক্তিবিজ্ঞানে যাকে সাধারণভাবে আমরা বচন বলি তাকে ব্যাকরণে বাক্য বলা হয়। যুক্তিবিজ্ঞানে সব বচন বাক্য কিন্তু সব বাক্যই বচন নয়। বাক্য ও বচনের মধ্যে পার্থক্য গুলি নিম্নে আলোচিত হল –
প্রথমত –
বচনের ক্ষেত্রে সত্যতা ও মিথ্যাত্ব নির্ণয় করা হয় । যেমন ‘মানুষ হয় মরণশীল‘ এক্ষেত্রে বচনটির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব আমরা নির্ণয় করি।
কিন্তু বাক্যের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করা হয় না। বাক্য সত্য বা মিথ্যা হয় না। সত্য বা মিথ্যা বাক্যের ধর্ম নয়। বাক্য কেবল শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হয়। যদি ব্যাকরণসম্মত হয় তবে বাক্য শুদ্ধ হয় আর ব্যাকরণসম্মত না হলে বাক্য অশুদ্ধ হয়।
দ্বিতীয়ত –
যুক্তিবিজ্ঞানে একমাত্র ঘোষক বাক্যই বচন হিসেবে গণ্য হয়।যেমন- সকল কবি হয় মানুষ এক্ষেত্রে সকল কবিকে মানুষ হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে।
কিন্তু ব্যাকরনের ক্ষেত্রে আমরা নানারকম বাক্য পাই। যেমন- আদেশমুলক, ইচ্ছামূলক, বিস্ময়সূচক, প্রশ্নসূচক ইত্যাদি এগুলি বচন প্রকাশ করে না। এক্ষেত্রে এই ব্যাকরণগত বাক্য গুলিকে আমরা বচন বলতে পারিনা।
তৃতীয়ত –
বচনের অন্যতম অংশগুলি হল – উদ্দেশ্য, বিধেয়, মানক ও সংযোজক। সংযোজক হল সেই চিহ্ন যা উদ্দেশ্য এবং বিধেয়কে যুক্ত করে।উদ্দেশ্য ও বিধেয়র মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে সংযোজক। যেমন ‘সকল কাক হয় কালো’ । এই সম্বন্ধ স্বীকৃতির বা অস্বীকৃতির হতে পারে।
কিন্তু বাক্যের দুটি অংশ – উদ্দেশ্য ও বিধেয়। যেমন ‘কাক কালো‘ বাক্যটির কেবল উদ্দেশ্য ও বিধেয় আছে।
চতুর্থত –
বচন সবসময় বর্তমান কালের হয় যেমন- ‘বিবেকানন্দ হন ব্যক্তি যিনি ছিলেন দার্শনিক’ তখন সেটি হবে বচন। কিন্তু বাক্য যে কোন সময় বা কালের হতে পারে।
কিন্তু এই বচনটিকে যদি এভাবে বলা হয় যে ‘বিবেকানন্দ ছিলেন দার্শনিক’ এটি বাক্য হলেও বচন নয়।
পঞ্চমত –
বচনের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে সংযোজক কে উল্লেখ করা হয়। বাক্যের ক্ষেত্রে সংযোজক কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় না। যেমন- ‘রাঘব ভালো ছেলে’ হল বাক্য। এক্ষেত্রে কোন সংযোজক কে উল্লেখ করা হয়নি।
কিন্তু যখন আমরা বলি ‘রাঘব হয় ভালো ছেলে’ তখন এটি একটি বচনে রূপান্তরিত হয়।এক্ষেত্রে ‘রাঘব‘ এবং ‘ভালো ছেলে‘ এর মধ্যে ‘হয়‘ কথাটি সংযোজক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
ষষ্ঠত –
বচনের ক্ষেত্রে গুন ও পরিমাণকে সর্বদা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয়।‘সকল কাক হয় কালো’ এই বচনটির ক্ষেত্রে গুণ- ‘হয়‘ এবং পরিমাণ- ‘ সকল‘ দুটোই উল্লেখ করা হয়েছে।
কিন্তু বাক্যের ক্ষেত্রে গুনও পরিমানকে সর্বদা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় না। যেমন –‘কাক কালো’ হল বাক্য। এখানে কোনপ্রকার গুণ ও পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি, কেবলমাত্র কাক কালো একথাই বলা হয়েছে।
সপ্তমত –
বাক্যের উৎস হল মনের ভাব। যে শব্দ বা শব্দসমষ্টি দ্বারা মনের ভাবকে প্রকাশ করা হয় তাকে বাক্য বলে।
কিন্তু বচনের উৎস হল অবধারণ। মনে মনে একাধিক ধারণাকে সংযুক্ত করাই হল অবধারণ। আর এই অবধারণকে ভাষায় প্রকাশিত করাই হল বচন।
অষ্টমত –
আবার অর্থহীন বাক্যও আছে, যেমন- ‘বাজারে যাচ্ছে রবিবার’। কিন্তু অর্থহীন বচন নেই।অনেক বাক্য আছে যা অভিন্ন অর্থবোধক হতে পারে, যেমন ‘সৌরভ একটি ক্রিকেটার‘ এবং ‘Sourav is Cricketer‘ বাক্য দুটি ভিন্ন ভাষার।
কিন্তু বাক্য দুটির অর্থ এক। বাক্যের এই অর্থগত দিক হল বচন। এইকারনে বলা যায় যে, ঘোষক বাক্যে যা প্রকাশিত হয় তাই বচন।
নবমত –
বাক্যের মাধ্যমে বচন প্রকাশ করা হয়। কিন্তু সব বাক্য বচন প্রকাশ করে না। একমাত্র ঘোষক বাক্য বচন প্রকাশ করে। অর্থহীন বাক্য আছে।
কিন্তু অর্থহীন বচন নেই। এইজন্য বলা যায় যে ঘোষক বাক্যে যা প্রকাশিত হয় তাই বচন।
আরো বলা যায়, বাক্যের মধ্যে যে সমস্ত অংশ থাকে তাদের সাজানোর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন নিয়ম থাকে না বাক্যের অংশগুলিকে ইচ্ছে মত সাজানো যায়।
কিন্তু বচনের মধ্যে যে সমস্ত অংশগুলো থাকে সেগুলোকে যথাযথ নিয়ম মেনে পরপর সাজাতে হয়। এই নিয়ম ভাঙ্গা চলেনা।
সুতরাং বাক্য এবং বচনের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও বাক্য ও বচনের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Proposition and Sentence) অর্থাৎ বৈসাদৃশ্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।
উদাহরণ
উপরে আমরা বাক্য ও বচনের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Proposition and Sentence) গুলিকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তার কিছু উদাহরণ নিম্নে উল্লেখিত হল –
ক) একটি বচনের উদাহরণ হল – ‘সকল ছাত্র হয় শিক্ষিত‘। এখানে ‘সকল‘ এবং ‘হয়‘ এদুটি পরিমাপক ও সংযোজক ব্যবহৃত হয়েছে। আবার ‘ছাত্র‘ এবং ‘শিক্ষিত‘ এদুটি উদ্দেশ্য ও বিধেয় দ্বারা একপ্রকার বচনকে প্রকাশ করা হচ্ছে।
একটি বাক্যের উদাহরণ হল – ‘রাম যায় বাজারে‘। এর ক্ষেত্রে কোন প্রকার আকার কে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি এবং কোন সংযোজক ও পরিমাপক এর ব্যবহার করা হয়নি।
খ) আমরা আমাদের মনের ভাবকে প্রকাশ করি বাক্যের মাধ্যমে। যেমন – ‘চিত্ত যেথা ভয়শূন্য’। যেখানে মনের ভাব প্রকাশ করতে কোন প্রকার রূপ বা আকার কে প্রয়োজন হয় না।
কিন্তু বচনকে আমরা এরূপে প্রকাশ করতে পারি না মনের একাধিক ধারণাগুলোকে সংযুক্ত করে আমরা বচনে প্রকাশ করি। যেমন – ‘সকল চিত্ত হয় এমন যা ভয়শূণ্য’।
উপসংহার
উপরিউক্ত সমস্ত আলোচনার ভিত্তিতে পরিশেষে এটা নিশ্চিত করা যায় যে, সব বচনই বাক্য কিন্তু সব বাক্যই বচন নয়। তবে কেবল বাক্য ও বচনের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Proposition and Sentence) বা বৈসাদৃশ্যই রয়েছে এমনটা নয়। বাক্য ও বচনের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য ও লক্ষ্য করা যায়। বাক্য ও বচনের মূল ভিত্তি সব সময় একই। সে কারণে বাক্য ও বচনের মধ্যে সাদৃশ্য বা মিল থাকা খুবই স্বাভাবিক।
তথ্যসূত্র (References)
- History of Western Philosophy: B. Russell
- History of Modern Philosophy: R. Falckenberg
- A Critical History of Modern Philosophy: Y.H. Masih
- A History of Philosophy: F. Thilly
- A History of Modern Philosophy: W.K. Wright
- A Critical History of Western Philosophy: D.J. O’Connor
- Internet Sources
প্রশ্ন – বচন ও বচনাকারের পার্থক্য কি?
উত্তর – বচন ও বচনাকারের পার্থক্য হল –
যে বিবৃতি সত্য বা মিথ্যা হতে পারে তাকে বচন বলে। যেমন সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব। অপরদিকে বচনাকার হলো পদ গ্রাহক প্রতীকের নির্দিষ্ট বিন্যাস। যেমন সকল s হয় p।
প্রশ্ন – A – বচনে কোন পদ ব্যাপ্য?
উত্তর – A বচনে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য, বিধয় পদ অব্যাপ্য।
প্রশ্ন – ‘যদি মেঘ করে তবে বৃষ্টি হয়’ এটি কোন বচন?
উত্তর – ‘যদি মেঘ করে তবে বৃষ্টি হয়’ এটি হল অনিরপেক্ষ বচন।
প্রশ্ন – ‘স্বার্থপর মানুষ আছে’ এটি কোন বচন?
উত্তর – ‘স্বার্থপর মানুষ আছে’ এটি হল নিরপেক্ষ বচন।
প্রশ্ন – ভাষা ও বচন এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
উত্তর – ভাষা ও বচন এর মধ্যে পার্থক্য হল –
ভাষা কে আমরা নিজের খুশি মত ব্যবহার করতে পারি। যেমন – ‘মেঘের দল ছুটে চলেছে’। কিন্তু বচনকে আমরা খুশি মত ব্যবহার করতে পারি না। বচনকে আমরা একটি নির্দিষ্ট আকারে ব্যবহার করি। যেমন – সকল যুবক হয় মানুষ।
- প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ চার্বাকদের উক্তিটি ব্যাখ্যা কর | Perception is the Only Source of Knowledge
- ব্যাপ্তি গ্রহের উপায় গুলি কি কি | What are the Ways to Identify of Vyapti
- চিরস্থায়ী শান্তি সংক্রান্ত কান্টের মতবাদ | Kant’s Doctrine of Perpetual Peace
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবতাবাদ | Rabindranath Tagore Humanism
- মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো | Features of Mahatma Gandhi’s Non-Violence Policy

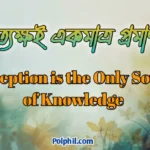


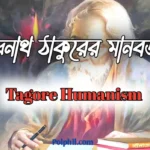
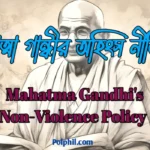
Valo legeche